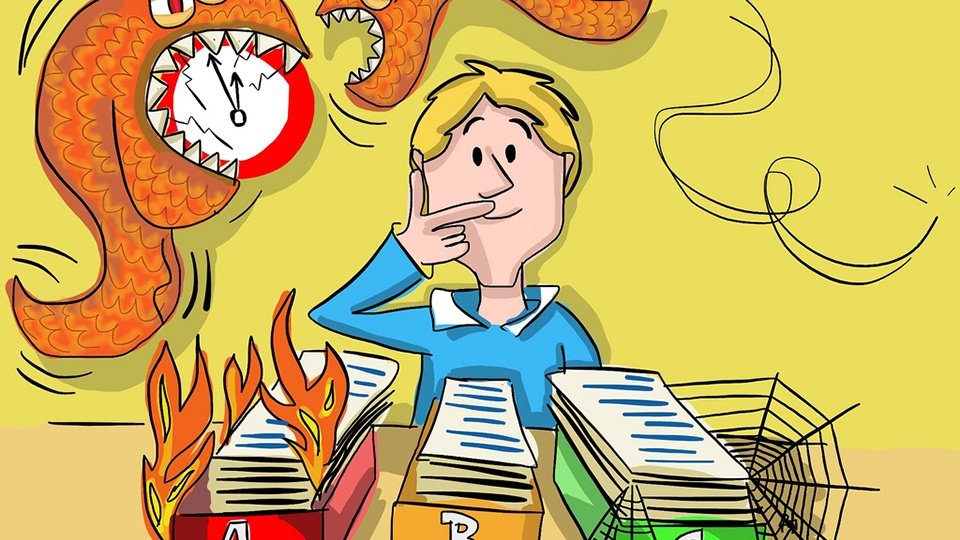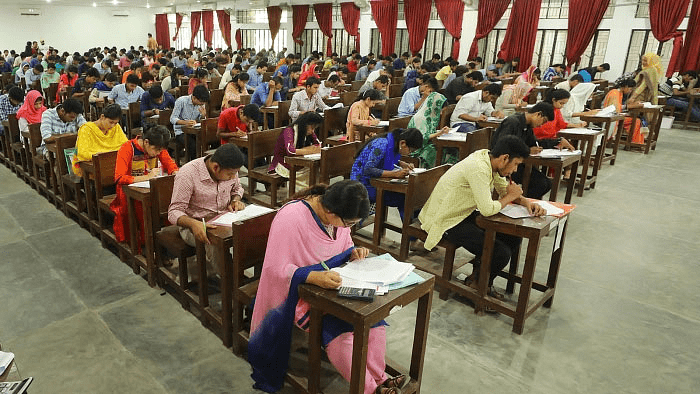নেদারল্যান্ড বললেই চট করে আমস্টারড্যাম বা দ্যা হেইগের কথা মাথায় চলে আসে। এই গল্পটা নেদারল্যান্ডের হলেও শহর দুটির কোনটার সাথে সম্পৃক্ত নয়। নর্থ সি’র কোল ঘেঁষে বেড়ে উঠা ছোট্ট শহর লেইডেন। এই শহরটাকে অক্টোপাসের মতো আকড়ে ধরেছে রিন নদী।
হেমিংওয়ে। ছাব্বিশ বছরের এক যুবক। জন্মসূত্রে আমেরিকান, তবে থিতু হয়েছে নেদারল্যান্ডে। পড়াশুনার বিষয় পদার্থবিজ্ঞান হলেও ছোটবেলা থেকে লেখালেখির প্রতি অগাধ আগ্রহ তার। হাইস্কুলে থাকাকালীন একটানা চারবছর অ্যানুয়্যাল রাইটিং কম্পিটিশনে প্রথম হয়েছিলো সে। লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পদার্থবিজ্ঞানের মতো এমন খটমটে একটা বিষয়ে স্নাতক করার পরও লেখালেখি থেকে দূরে সরে আসেনি। ছাত্রদের সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘ম্যায়ার’ এর প্রতি সংখ্যায় হেমিংওয়ের একটা লেখা সবসময়ই থাকতো। এই লেখালেখির সুবাধে ক্যাম্পাসে তার জনপ্রিয়তাও ছিল বেশ। যাহোক, পড়াশুনা শেষে স্থানীয় এক দৈনিকে সাব এডিটর হিসেবে যোগ দিয়েছে হেমিংওয়ে। সাহিত্য পাতাটা সে দেখে। বিভিন্নজন লেখা পাঠান, সেসব লেখা ঘষামাজা করা তার কাজ। অফিসে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। যখন খুশি যায়, যখন খুশি আসে। অধিকাংশ সময়ই বাইরে থেকে অফিসের কাজ সারে। বাইরে মানে, তার প্রিয় উডস রেস্তোরাঁয়।
লেইডসোয়েগে একা একটা বাসায় থাকে হেমিংওয়ে। সেখান থেকে গাড়িতে করে উডসে আসতে বার মিনিটের পথ। প্রায় প্রতিদিনই একই সময়ে আসে, একই টেবিলে বসে এবং একই খাবার অর্ডার করে – ব্রুশ্যাটা, পানি এবং লাল চা। রিন নদীর তীরে এই রেস্তোরাঁটার অবস্থান। এর ছাদের উপর একটা বহুদিনের পুরোনো উইন্ডমিল আছে বলে সহজেই দূর থেকে দেখে চেনা যায়।
রয় হেমিংওয়ের পুরোনো বন্ধু। একসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছে। তার বাবামা ভারতীয়। নেদারল্যান্ড এসেছে অন্তত দশক দুয়েক আগে, যখন তার বয়স চার কি পাঁচ। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের কিছুই তার স্মৃতিতে নেই। সে হিশেবে পুরোদস্তর ডাচ বলা চলে। এখন ফুলটাইম ফটোগ্রাফার আর পার্ট টাইম হেমিংওয়ের আড্ডার সঙ্গী। রয় যতক্ষণে হেমিংওয়ের সাথে যোগ দেয় ততক্ষণে তার অফিসের নিয়মিত কাজ শেষের দিকে। তাই বাকি সময় জমিয়ে আড্ডা দেয়া যায়। সাধারণত আড্ডার বিষয় সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি এসব। আর মাঝে মাঝে মেয়ে সংক্রান্ত বিষয়াদি।
রয় সেদিন আসেনি। অফিসের কাজও দ্রুত শেষ হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত একটা এসাইনম্যান্ট শেষ করার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু কোনোভাবেই মাথা থেকে লেখাটা বের হচ্ছিলোনা। হাঁসফাঁশ করছে আর নিজের চুল টানাটানি করছে। এর মধ্যে কারা যেন তাকে দেখে সশব্দে হেঁসে দিলো। ল্যাপটপ থেকে ডানে চোখ ফিরাতেই চোখে পড়ে একজন রমণী। পাশের টেবিলে একা বসে আছে। আসলে মেয়েটা হাসেনি, হেসেছে অন্যকেউ। বেশ লম্বা-চৌড়া, চেহারা লাবণ্যময়, আর পরনে মার্জিত পোশাক। প্রথম দেখাতেই চোখ আঁটকে যাওয়ার মতো। কি যেন ভাবছে আর আনমনে কিন্ড্যালটা নাড়াচাড়া করছে। যাহোক, চোখ ফিরিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো হেমিংওয়ে।
একটু পর রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাবে। সবকিছু গোছগাছ করার প্রক্রিয়া চলছে। হেমিংওয়েও বের হবে, এমন সময় হঠাত একটা মেয়ে দৌড়ে আসলে। ভুলে কিন্ড্যালটা নাকি ফেলে গেছে, সেটা নিতে এসেছে। প্রথম দেখাতেই চিনে ফেললো হেমিংওয়ে। এইতো সেই মেয়েটা। কাউন্টার থেকে কিন্ড্যালটা সংগ্রহ করার পর বের হওয়ার পথে সামনাসামনি দেখা। অনেকটা সেধে গিয়ে হাই-হ্যালো করলো হেমিংওয়ে। কিছুক্ষন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কথাও হলো। মেয়েটার বেশ আগ্রহ নিয়ে আলাপচারিতা করলো। তার নাম ক্রিস্টিন। ডাচ নাগরিক। লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতক করছে। উডস সম্পর্কে জানতে পারে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খানিকটা দূরে হওয়ায় সাধারনত উডস-এ আসা হয়না। আজকে কি ভেবে এক ফাঁকে চলে এসেছে।
অনেকদিন ক্রিস্টিনের দেখা নেই। হেমিংওয়ে নিজের মতো কাজ করে যাচ্ছে। রয় যখন মন চায় আসে, আড্ডা দেয়। যখন মনে চায়না, আসেনা। এভাবে প্রায় মাস খানেক পেরিয়ে গেলো। কোন এক বিকেল বেলা। হেমিংওয়ের কাজ শেষ। রয়ের সাথে আড্ডা চলছে। আড্ডার বিষয় ফরাসি বিপ্লব। সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, উয়াদারনীতিবাদ আর নেপোলিয়ায়নের উত্থান – এসব বিষয়ে ইনটেন্স বিতর্ক-আলোচনা চলছিল দুজনের মধ্যে। হঠাত কেউ একজন হেমিংওয়ের নাম ধরে ডাক দিলো। মাথা উঁচু করে একবার তাকাতেই চিনে ফেলে – এতো ক্রিস্টিন! হেমিংওয়ে পরিচয় করিয়ে দেয় – ক্রিস্টিন, এ হচ্ছে আমার বন্ধু আর আড্ডার সঙ্গী, রয়। রয়, এ হলো ক্রিস্টিন, আমার বান্ধবী। যার কথা সেদিন তোমাকে বলেছিলাম।
ক্রিস্টিন জানতে চায়, তা কি নিয়ে এতো মনোযোগ দিয়ে গল্প হচ্ছিলো শুনি…
অবশ্যই, ফরাসি বিপ্লব, হেমিংওয়ে জবাব দেয়।
ফরাসি বিপ্লব? সিরিয়াসলি? এটাও আড্ডার বিষয় হতে পারে? ক্রিস্টিন জানতে চায়।
রয় বলে উঠে, এতো অবাক হওয়ার কি আছে? প্রতিদিনই তো এই কাজটা করি। যেমন ধরো গতোকাল আলাপ করেছি রেনেসাঁস নিয়ে। তার আগের দিন বার্লিন দেয়ালের উত্থান পতন আর তারপরদিন…
থাক থাক থাক, আর বলতে হবেনা – এই বলে থামিয়ে দেয় ক্রিস্টিন।
আলোচনায় বিষয় বদলে যায়। হেমিংওয়ে আর রয় বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছে বেশ কিছুদিন হলো। এর মধ্যে ক্যাম্পাস অনেক বদলে গেছে। ক্রিস্টিনের উপস্থিতিতে সেদিনের আড্ডাটা বেশ জমে উঠে। স্মৃতিচারণ চলে ক্লাসের নানান গল্প আর মজার ঘটনাদি নিয়ে। এরপর থেকে যখনই সময় পায়, উডসে চলে আসে ক্রিস্টিন। এভাবে একসময় হেমিংওয়ে আর রয়ের আড্ডার গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী হয়ে উঠে সে। সারাদিন যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে, আর বিকালে বেলা উডসে এসে আড্ডা দেয়। এর মধ্যে আড্ডার বিষয়েও বেশ বিচিত্রতা এসেছে। সিরিয়াস বিষয়ের পাশপাশি এখন খুব তুচ্ছ বিষয় নিয়েও তিনজনের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ হয়।
তবে ক্রিস্টিনের প্রভাব শুধু আলোচনার বিষয়ে পড়েছে সেটা বললে ভুল বলা হবে। তার প্রভাব পড়েছে হেমিংওয়ের মনেও। দেখতে সুন্দরী নিঃসন্দেহে। তার উপর সিয়িয়াস কিংবা তুচ্ছ বিষয়ে ক্রিস্টিনের দৃষ্টিভঙ্গি বা আলোচনার ধরণ সত্যি অনন্য। নিয়মিত গালগল্পের মাঝেমাঝে ব্যক্তিগত বিষয়াদি উঠে আসে। বাড়তে থাকে হেমিংওয়ের অনুভূতিগুলোও। নিজের ভেতর এতোকিছু ঘটছে, কাউকে তো বলতে হয়। ক্রিস্টিনের অনুপস্থিতিতে রয়ের সাথে একদিন কথাগুলো ভাগাভাগি করে হেমিংওয়ে। রয় তার কথা শুনে বেশ শকড হয়। তারও ভালো লাগে ক্রিস্টিনকে। সেও এতোদিন কাউকে বলেনি কিছু। এরমধ্যে তার বন্ধুর ভালোলাগার কথা শুনে কুলিয়ে উঠতে পারেনা। অনেকটা জোর করে মাথা থেকে বিষয়টা ঝেড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে সে। হাজার হোক, বন্ধু তো। সে চায়না এই বিষয়টা নিয়ে তাদের বন্ধুতে টান পড়ুক। বরং রয় হেমিংওয়েকে নানান সময় পরামর্শ দেয়, চেষ্টা করে বিষয়টাকে সহজভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।
প্রতিদিন বিকেল বেলা হয়, রয় আসে, কোন কোন দিন ক্রিস্টিনও আসে, জমে উঠে আড্ডা। ক্রিস্টিন থাকলে অনেক কিছু নিয়েই আলাপ হয়। কিন্তু না থাকলে ক্রিস্টিনই হয়ে উঠে দুজনের আলোচনার বিষয়। হেমিংওয়ের এই অবস্থা দেখে রয় পরামর্শ দেয় ক্রিস্টিনকে সোজাসাপ্টা তার অনুভুতির কথা জানিয়ে দেয়ার। হেমিংওয়েও তাই ভাবছে।
এর মধ্যে গ্রীষ্ম চলে এসেছে। চারদিকে মিষ্টি রোদ। সতের ডিগ্রী সেলসিয়াস বলা যায়। ক্যালেন্ডার মতে চব্বিশ জুলাই থেকে পাঁচ সেপ্টেম্বর একটা লম্বা ছুটি পাওয়া গেলো। সবমিলিয়ে ঘুরাঘুরির উপযুক্ত সময়। তিনবন্ধু পরিকল্পনা করে ফ্রান্সের মুজা গ্রামে তারা এই গ্রীষ্মটা কাটাবে। মুজা ফ্রান্সের দক্ষিণের একটা শহর। শিপ্ল সাহিত্যে বেশ সমৃদ্ধ এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী পিকাসো। আর সেখানেই ক্রিস্টিনকে ভালো লাগার কথা জানাবে হেমিংওয়ে।
পরদিন বিকাল বেলা। হেমিংওয়ে তো আছেই। আছে রয় আর ক্রিস্টিনও। মুজা গ্রামের কথা শুনে ক্রিস্টিন এক পায়ে খাড়া। গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হতেই পারেনা। হেমিংওয়ের ভাষায়, “এতো সুন্দর করে সাজানো, যেন পুরো গ্রামটাই একটা বিশালাকার শিল্পকর্ম। পিকাসোর ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে ধারন করে রেখেছে এই গ্রাম।” গ্রীষ্মের ছুটি আসতে বেশীদিন বাকি নেই। প্রত্যেকেই যে যার মতো কেনাকাটা সেরে নিলো। আরেকদিন বসে ঠিক করলো কোথায় কখন কি করবে সেটা। হেমিংওয়ের উৎসাহ সবার চেয়ে বেশী। তেমন কিছু কিনেনি সে। বিশেষ কিছু বলতে নিজের জন্য ক্রিস্টিনের পছন্দের নীল রঙয়ের একটা ফ্লোরাল শার্ট আর একটা কিন্ড্যাল ওয়াসিস। কিন্ড্যালটা নিজের জন্য নয়, ক্রিস্টিনের জন্য কিনেছে।
গ্রীষ্মের ছুটি চলে এলো। পূর্ব পরিকল্পনা মতো সকাল নয়টায় সবার পার্কেরেন লেইডেন-এ চলে আসার কথা। রয় আর ক্রিস্টিন ঠিক সময়ে চলে এসেছে। হেমিংওয়ে এলো সবার শেষে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নাকি ব্যাকপ্যাক ছাড়াই চলে এসেছিলো ভুলে। অর্ধেকটা পথ চলে আসার পর হুশ ফিরে তার। ফের গিয়ে ব্যাগ নিয়ে আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো।
যাহোক, দীর্ঘ ষোল ঘন্টার জার্নি। কেমন লাগছে? রয় জানতে চায়।
সুপার এক্সাইটেড! ড্রাইভিং নিয়েও সমস্যা হওয়ার কথা না। তিনজনে ভাগাভাগি করে চালিয়ে দেয়া যাবে। ক্রিস্টিন জবাব দেয়।
আমরা আমরাই তো। গল্প করতে করতে পার হয়ে যাবে। যোগ করে রয়।
ব্রাসেলস, লুক্সেমবার্গ, জেনিভা হয়ে কান। সেখান থেকে মুজা একদম কাছেই। এই পথে কখনো যাইনি। জানায়, হেমিংওয়ে।
চলো, শুরু করা যাক বলে সবাই গাড়িতে উঠে পড়লো। রয় ড্রাইভিং করছে শুরুতে। হেমিংওয়ে আর ক্রিস্টিন পেছনের আসনে বসা। গাড়ি চলছে… ইতিমধ্যে বেলজিয়ামে প্রবেশ করেছে গাড়ি। শুরুতে অনেক হই হুল্লোড় দেখা গেলেও ঘন্টা দুয়েক পর উত্তেজনায় ভাটা পড়লো। ততক্ষোনে পেছনের দুইজন ঘুমিয়ে পড়েছে। রয় বেচারা ড্রাইভিং সিটে। তাই ঘুমোতে পারছেনা। ওদিকে অন্য দুই বন্ধু ঘুমিয়ে আছে দেখে সহ্যও হচ্ছেনা। রয়ের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো। খালি রাস্তাতেই নব্বই মাইল বেগে চলা গাড়িতে সজোরে ব্রেক কষলো সে। প্রচন্ড ভয়ে ঘুম থেকে হুমড়ি খেয়ে উঠে পড়ে হেমিংওয়ে আর ক্রিস্টিন। আর তাদের অবস্থা দেখে হাসতে থাকে রয়। কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে ট্রে তে রাখা পানির বোতল ছুঁড়ে মারে রয়ের দিকে। রয়ের গায়ে লাগেনি বোতল, উল্টো মুখ খুলে পানি ছিটকে সামনে রাখা হেমিংওয়ের ব্যাগে গিয়ে পড়েছে। যাহোক, ছোটখাটো একটা ফাইট শেষে সবাই আবার চাঙ্গা হয়ে গেলো।
গাড়ি চলছে তো চলছেই… এতোক্ষনে আরও অনেকটু পথ পাড়ি দিয়েছে। মাঝপথে বুর্গ-এন-ব্রিস এর একটা রেস্তোরায় তারা দুপুরের খাবার সেরে নিলো। সুন্দর পরিবেশ। সামনের দিকটা খোলা সবুজ প্রান্তর। খাওয়াদাওয়া সেরে সেখানটায় কিছুক্ষন বসার পর আবার গাড়িতে উঠলো তারা। এবার চালকের আসনে হেমিংওয়ে। গাড়ি চালাচ্ছে আর মাঝে মাঝে এস্প্রেসোর কাপে চুমুক লাগাচ্ছে। ঘুম কাটানোর জন্য এই প্রচেষ্টা। সুইজারল্যান্ড সীমান্ত পেরিয়ে গেছে গাড়ি। জিপিএস বলছে গাড়ি তখন ট্রেফোর্ট নামের একটা জায়গায়। এর মধ্যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে এলো। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ। তবে ভয়ের কিছু নেই। পাহাড়গুলো এতোটা উঁচু নয়। গাড়িতে ফাইভ হান্ড্রেড মাইলস বাজছে। হেমিংওয়ে ভলিউমটা বাড়িয়ে দিলো। দিনের আলো থাকলো ভীষণ ভালোভাবে উপভোগ করা যেতো। এনিয়ে ক্রিস্টিনকে হা হুতাশা করতে দেখা গেলো। হেমিংওয়ে বললো, “চিন্তা করোনা, ক্রিস্টিন। ফেরার সময় যথেষ্ট আলো থাকবে। তখন গাড়ি থামিয়ে প্রান ভরে দেখতে পারবে।” কথা শুনে ক্রিস্টিন মৃদু হাসলো।
হেমিংওয়ে অনেক্ষন ধরে ড্রাইভ করছে। সে বললো, “ক্রিস্টিন, প্রস্তুত হও। সামনে একটা কফিশপ আছে। ওইখান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়াই আমার কাজ। সেখানে বসে কফি খেয়ে তারপর…” কথাটা শেষ করতে পারলোনা হেমিংওয়ে, বিপরীত দিক থেকে আরেকটা গাড়ি এসে ধাক্কা দিলো, দুইবার উল্টে গাড়িটা একটা বড় গাছে গিয়ে আটকালো। যেন মুহূর্তেই সব তচনচ হয়ে গেছে। পেছনের সিট থেকে কোনোভাবে বের হয়ে আসলো ক্রিস্টিন আর রয়। তাদের তেমন একটা আঘাত লাগেনি। রয়ের বা চোখের উপরে দিকটায় কাচ লেগে রক্ত বের হচ্ছে। ক্রিস্টিনের দুই পায়ে খানিকটা চোট লেগেছে। ভাগ্য কিছুটা ভালো, গাড়িটা গাছে আঁটকে ছিলো। না হয়… আচ্ছা, হেমিংওয়ে কই? মনে পড়তেই তড়িঘড়ি করে সামনের দরজা খুলে হেমিংওয়েকে টেনে বের করে তারা দুজন। সারা মুখে রক্ত। চেহারা দেখে বুঝার অবস্থা নেই। পেটে দুটো ভাঙ্গা কাচের টুকরো ঢুকে পড়েছে। রয় বুঝতে পারছেনা কি করবে। অজানা অচেনা চারপাশ। এর মধ্যে খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ চলে আসে। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের এক হাসপাতালে।
হাসপাতালেই সে রাত পার হলো। রয় আর ক্রিস্টিন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে সেরে উঠলো বটে, তবে ঘুমাতে পারলোনা চিন্তায়। হেমিংওয়েকে নিয়ে যাওয়া হইয়েছিলো আই.সি.ইউ-তে। পরদিন আসলো খবরটা – বাঁচানো যায়নি হেমিংওয়েকে। শুনে যেন তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তারা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছেনা হেমিংওয়ে আর নেই। কি ভেবেছে, আর কি হচ্ছে এসব?
হাসপাতাল থেকে রিলিজ করতে হলে কিছু কাগজপত্র লাগবে। ক্রিস্টিন হেমিংওয়ে’র ব্যাগ চেক করে। খুজতে গিয়ে ব্যাগে নীল খামের ভেতর একটা চিঠি খুঁজে পায়। কিন্তু চিঠি পড়ার সময় এখন নয়। যে কাগজটা খুঁজছিল সেটা নিয়ে হাসপাতালের রেসিপশনে গেলো। প্রয়োজনীয় ফরমালিটি সেরে হেমিংওয়ের লাশ নিয়ে ফিরছে ক্রিস্টিন আর রয়। তাদের চোখে মুখে অন্ধকার। কারও মুখে একটা শব্দ নেই। কতো স্মৃতি, কতো পরিকল্পনা মুহূর্তে শেষ হয়ে গেলো। মনে পড়তেই দু চোখে শুধু পানি ঝরছে শুধু।
ক্রিস্টিনের মনে পড়ে হেমিংওয়ের ব্যাগে থাকা চিঠিটার কথা। খুঁজে নিয়ে নীল খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে সে। খুব যত্ন করে হেমিংওয়ের নিজ হাতে লেখা চিঠি। তাতে লেখা –
//
প্রিয় ক্রিস্টিন,
আমার দু চোখের আলো, আমার রাজ্যের সব মুগ্ধতা।
এই প্রানের বিনিময়ে হলেও আমি তোমাকে চাই।
তুমি কি আমার হবে?
ইতি,
হেমিংওয়ে।
//